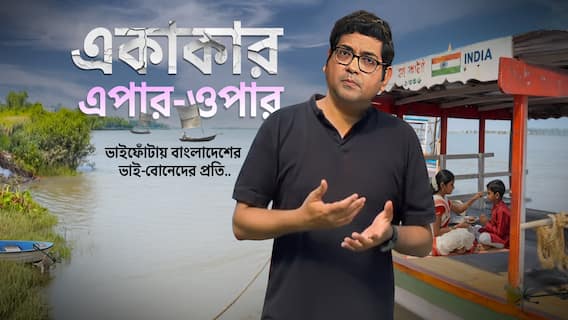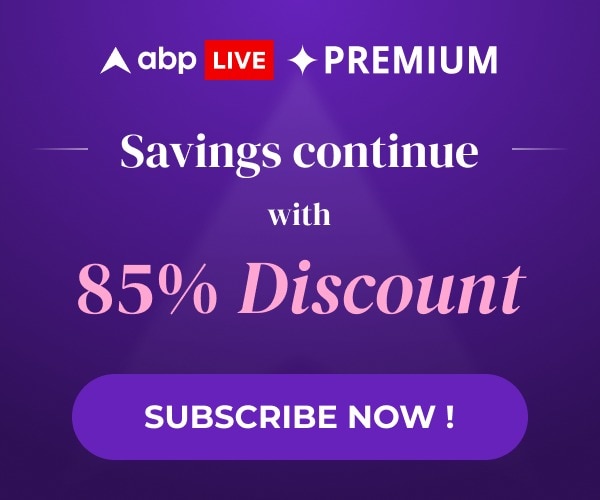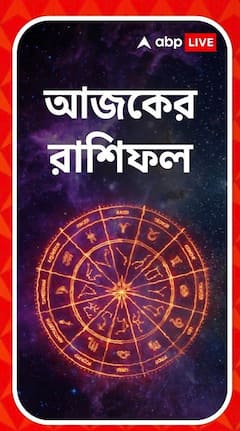Jawaharlal Nehru: উদীয়মান দেশের অগ্রদূত: নেহরুর ভারত-ভাবনা

জওহরলাল নেহরু, ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর জন্ম (Jawaharlal Nehru)। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নন শুধু, এখনও অবধি দেশের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রীও তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নেহরু, সেই সময় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উল্লাস যেমন ছিল, তেমনই অত্যন্ত কঠিন এবং অভূতপূর্ব সন্ধি ক্ষণে দাঁড়িয়েছিল দেশ (India Under Jawaharlal Nehru)। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েই ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর মধ্যরাতে যখন সংবিধান সভা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন নেহরু, তাতে ‘নিয়তির সঙ্গে ভারতের বোঝাপড়ার’ উল্লেখ ছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সেই স্বপ্নপূরণের মুহূর্তে যখন বিভোর গোটা দেশ, সেই সময় সংসদভবনেই নেহরু উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারিগর, মোহনদাস গান্ধীই স্বাধীনতা উদযাপনে গরহাজির। কারণ সেই সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছিন্নভিন্ন কলকাতায় ছিলেন গান্ধী। ভারত এবং পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী সংঘাত যে সারি সারি লাশ, দৃশ্যমান ক্ষতের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বেনজির শরণার্থী সঙ্কট, দেশভাগের ক্ষতের পাশাপাশি নেমে আসে যুদ্ধের খাঁড়া। তার ঠিক ছয় মাস পরই আততায়ীর গুলি ঝাঁঝরা করে দেয় গান্ধীকে। শোকাচ্ছন্ন করে ফেলে গোটা দেশকে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর গুরুদায়িত্ব যেমন হাতে ছিল, তেমনই দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, পীড়িতদের সান্ত্বনাপ্রদানের ভারও তখন নেহরুর কাঁধেই। তারই মধ্যে গোটা বিশ্বের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠা, জাতির জনক হয়ে ওঠা, আধুনিক যুগের গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট উপমা পওয়া, গান্ধীর শেষকৃত্য তদারকিও দায়িত্ব বর্তায়। শোনা যায়, গান্ধীর শেষকৃত্যের প্রস্তুতি চলাকালীন কার্যতই দিশাহারা হয়ে পড়েন নেহরু। গান্ধীর উপদেশ নিতে অভ্যস্ত নেহরু শেষকৃত্যের মাঝেই বলে ওঠেন, “চলো বাপুর কাছে যাই। উনি রাস্তা বাতলে দেবেন।”
সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরুর সামনে ছিল অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার লক্ষ্য। তৎকালীন অন্য ঔপনিবেশিক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের তুলনায় নেহরুর যাত্রাপথ ছিল কঠিনতর। গ্রামেগঞ্জে, শহরে, নগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৩০ কোটির বেশি জনসংখ্যা, যা বিস্ময়কর ভাবে বৈচিত্রপূর্ণ, জাত, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সবের নিরিখেই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অধিকাংশ ভারতীয়ই সেই সময় দরিদ্রসীমার নিচে ছিলেন, যা ২০০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন শোষণেরই ফলশ্রুতি ছিল এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শাসকের হাত থেকে উত্তরাধিকার বাবদ পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে গঠিত রাজনৈতিক পরিকাঠামো। সেখান থেকে একটি দেশকে আধুনিক ‘সার্বভৌমিক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’ করে তোলার যাত্রা, টানা একবছরের নিরন্তর পরিশ্রম, তর্ক-বিতর্ক পেরিয়ে ভারতীয় সংবিধানের রচনা গোটা বিশ্বে নজিরবিহীন। এ ছাড়াও অনেক কিছুই নতুন ছিল ভারতের কাছে। ইংরেজ আমলের অবিভক্ত ভারত যেমন ছিল, তেমনই ৫৬২টি দেশীয় রাজ্য, যার মাথায় আবার ছিলেন বংশানুক্রমিক ভাবে শাসনকার্য চালিয়ে আসা রাজারা। যেন তেন প্রকাপে সেখানকার নাগরিকদের ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চ্যালেঞ্জও ছিল সামনে। ইতিহাস অনুরাগীরা এই প্রক্রিয়াকে ‘ভারতীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণ’ বলে উল্লেখ করেন। তবে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতকে তুলে ধরার চ্যালেঞ্জ নেহরু এবং কংগ্রেসের জন্য যে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বললে অত্যূক্তি হয় না।
নেহরুর সময়কাল নিয়ে কাটাছেঁড়ার অন্ত নেই যদিও। নেহরুর নেতৃত্বে আধুনিক ভারতের সূচনা, বিশ্বমঞ্চে তাঁর প্রবেশের সুফল-কুফল থেকে খোদ নেহরুর সাফল্য, ব্যর্থতার খতিয়ান তৈরি করতে পারেন যে কেউ। কিন্তু ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কৃতিত্বের অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। কারণ সেই সময় গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বিক ভোটাধিকার প্রয়োগে বিশ্বের কোনও দেশই নজিরবিহীন সাফল্য পায়নি। বিশেষ করে দেশভাগের ভয়াবহতা এবং ক্ষত যেখানে তখনও দগদগে হয়ে ছিল মানুষের মনে, তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছিল সর্বত্রই। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোটদান করেন ১৬ লক্ষ ভারতীয়, যা ছিল দেশের তৎকালীন মোট ভোটারের প্রায় ৪৫ শতাংশ। অথচ ১৯৫১ সালে প্রথম বার নির্বাচনের সময় দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মোটে ১৮ শতাংশের সামান্য বেশি। এর পর ১৯৫৭ এবং ১৯৬৪ সালের মে মাসে নেহরুর মৃত্যুর আগে, ১৯৬২ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস কাটিয়ে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কোনও দেশে এমন নজির নেই। গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি নেহরুর নিষ্ঠার প্রমাণের দলিল হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে এই পরিসংখ্যান। এ কথাও সত্য যে, নেহরুর শাসনকালে আট বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। ১৯৫৯ সালে কেরলে ইএমএস নাম্বুরিপাদের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার উৎখাতের সিদ্ধান্তকেও নেহরুর অসহিষ্ণুতা এবং ব্যর্থতার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন অনেকে।
নেহরু সম্পর্কে এমন ধারণা থাকতেই পারে অনেকের। নেহরুর ভারত-নীতি এবং ভাবনাকে যতই সংক্ষিপ্ত করে তোলার প্রচেষ্টা হোক না কেন, ততই তার পরিধির বিস্তৃতিই ঘটবে। উত্তরাধিকার সূত্রে ইংরেজ শাসকের কাছ থেকে সংসদীয় প্রতিষ্ঠান পায় ভারত। নেহরুর নেতৃত্বে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও যত্ন-সহকারে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, ইতিহাস, নীতি এবং সংবেদনশীলতার ছোঁয়া রাখার উদ্দেশ্যও ছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে। সামগ্রিক ভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থিতিশীল এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। উচ্চতর আদালতগুলি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের তরফে হস্তক্ষেপ, বাধা-বিপত্তি ছাড়াই স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় সংবাদমাধ্যম। লোকসভার তৎকালীন তর্ক-বিতর্কই প্রমাণ যে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে এলেও, বিরোধীদের কখনও হেয় করা হয়নি। বরং খোদ নেহরু এবং তাঁর মন্ত্রীদেরই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হতো। এমনকি প্রথম বার সাধারণ নির্বাচনের আগেই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভোটপ্রক্রিয়ার তদারকির জন্য প্রতিষ্ঠা হয় নির্বাচন কমিশনের। নেহরুর আমলে ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রমাণে ভারত থকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পৃথক দেশ হিসেবে গড়ো ওঠা পাকিস্তান, এবং ওলন্দাজ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ টানা যেতে পারে। নাগরিকের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের উপর কোনও ভাবে যাতে সেনার প্রভাব বা কর্তৃত্ব না থাকে, তা নিশ্চিত করা হয় ভারতে। নেহরুর সাফ যুক্তি ছিল যে, সেনাবাহিনী নাগরিক দ্বারা নির্বাচিত সরকারের নির্দেশ মেনে চলবে,যে কোনও গণতন্ত্রের মূল নীতি তেমনই হওয়া উচিত।
কেউ এই শিরায় যেতে পারে, তবে নেহরুভীয় ব্যবস্থার অধীনে ভারতের ধারণা এবং নীতিকে সংক্ষেপে যতই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হোক না কেন তা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। ভারত ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সংসদীয় প্রতিষ্ঠান পেয়েছিল এবং নেহরুর অধীনে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও লালন-পালন করা হয়েছিল, কখনও কখনও তাদের ভারতীয় অবস্থার প্রতি আরও প্রতিক্রিয়াশীল করার উদ্দেশ্যে এবং এমনকি ভারতের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের প্রতি ভারতীয় নীতি বা সংবেদনশীলতা প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি, সামগ্রিকভাবে, স্থিতিশীলতা এবং পরিপক্কতা দেখিয়েছে, উচ্চতর ভারতীয় আদালতগুলি স্বাধীন রায় দেওয়ার ক্ষমতা দেখিয়েছে, এবং সংবাদপত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাধা ছাড়াই তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করেছে। সেই সময়ের লোকসভা বিতর্কগুলি দেখায় যে, যদিও কংগ্রেস পার্লামেন্টে অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু বিরোধীরা কোন ওয়াক-ওভার ছিল না এবং নেহেরু ও তার মন্ত্রীদের প্রায়ই পরীক্ষা করা হয়েছিল। সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা এই সত্য দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিপরীতে, বা (বলুন) ইন্দোনেশিয়ায় যা ডাচ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক সরকারের উপর কোনো প্রভাব প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়ে, নেহেরু কঠোরভাবে নিশ্চিত করেছিলেন, যে কোনো গণতন্ত্রের মতোই তা করতে হবে, সামরিক বাহিনী বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করবে।
তাই বলে নেহরুর শাসনকালে ভারত সাম্প্রদায়িক অশান্তি থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে দেশভাগকে ঘিরে ঘটে চলা হত্যা কমে যায়। তবে দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও খামতি, সন্দেহ থাকা অনুচিত বলেই মনে করতেন নেহরু। সেই সময় যত সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছে, অধিকাংশই ছিল ছোট এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ১৯৬১ সালে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরেই একমাত্র সাম্প্রদায়িক অশান্তি গুরুতর আকার নেয়। ব্যবসায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের উন্নতি ভাল ভাবে নেননি হিন্দুদের একাংশ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আঁচ নেভাতে নেহরুর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। প্রখ্যাত মার্কিন লেখক নরম্যান কাজিনস-এর লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি থামাতে নিজে, ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করেন নেহরু। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে তিনি খোদ রাস্তায় নামেন। নিজে তা চাক্ষুষ করেছেন বলে জানান নরম্যান। তর্কের খাতিরে এ কথা বলা যায় যে, জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদারক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন নেহরু। কিন্তু সাহস করেই বলছি, নিছক উদারতা থেকে নয়, গান্ধী-সহ ভারতের সন্ত-ঐতিহ্য থেকেই এই শিক্ষা পেয়েছিলেন নেহরু। এ ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের (সেই সময়কার পরিচয়) অধিকারের প্রসঙ্গ তুলে ধরতে পারেন নিন্দুকরা। যুক্তি দিতে পারেন যে, নেহরুর আমলে তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত হয়নি। কিন্তু এর সপক্ষে তেমন প্রমাণ মেলে না। তবে এক কথা সত্য যে, সাংবিধানিক ভাবে দলিতদের অধিকার, সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হলেও, পূর্ণ নাগরিক হিসেবে সমাজে তাঁদের স্বীকৃতি পেতে অনেক সময় লেগেছিল, অন্তত বিআর অম্বেডকরের স্বপ্নের তুলনায় তার গতি অনেকটাই শ্লথ ছিল।
এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যায় যে, নেহরু যেমন ব্যক্তি নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানাধিকারে বিশ্বাস করতেন, তেমনই নেহরুর আমলের ভারত তাঁর উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিল। কেরলের নাম্বুরিপাদ সরকারকে উৎখাতের জন্য তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, নেহরু অসহিষ্ণু, কর্তৃত্ববাদী ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং তাঁর আমলে গড়ে ওঠা সহিষ্ণুতা এবং ভিন্নমতের গুরুত্ব পাওয়াকে আলাদা করে দেখতে হবে। নেহরুর সরকারে সহিষ্ণুতার উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য এবং সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভাসন ঘটে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল নেহরুর সরকার। নেহরুর প্রায় প্রতিটি লেখায় ভারতকে আধুনিক করে তোলার, বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র করে তোলার উল্লেখ মেলে। আইআইটি খড়্গপুর (১৯৫১), আইআইটি বম্বে (১৯৫৮), মাদ্রাস (১৯৫৯), কানপুর (১৯৫৯) এবং দিব্বি (১৯৬১)-স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত যে প্রতিষ্ঠানগুলি, তা গড়ে ওঠে নেহরুর হাতেই। আজও দেশের উচ্চশিক্ষার সেরা ঠইকানা হয়ে রয়েছে সেগুলি। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (১৯০৯)-এ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।
আতিথেয়তার যে সংস্কৃতি এবং নীতি, নেহরুর আমলে তার মাত্রা ছিল ভিন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দৃঢ় ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নিবেদিত ছিলেন নেহরু। ইদানীং কালে লাগাতার শোনা যাচ্ছে, নেহরু নাকি বড্ড বেশি পশ্চিমি সংস্কৃতি ঘেঁষা ছিলেন, সাধারণের সংস্পর্শের বাইরে ছিলেন, ধর্ম নিয়ে সাধারণ ভারতীয়দের অদম্য তৃষ্ণা বোঝেননি তিনি! কিন্তু এই যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল এবং তেমনই ভারতীয় সমাজজীবনে ধর্মকে নেহরু অস্বীকার করেন, এমন বলাও অসংবেদনশীলতার পরিচয়। বরং নেহরু যে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন, তা অনেক গভীরে প্রোথিত ছিল। ধর্মকে প্রত্যাখ্যান নয়, বরং ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করে তোলার পরিপন্থী ছিল। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলে, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বাকিদের তুলনায় হিন্দুদের প্রাধান্য দেওয়ার যে ধারণা, তার বিরুদ্ধে ছিলেন নেহরু। সেই কারণেই ১৯৫১ সালে তৎকালীন নবনির্মিত সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনে রাজেন্দ্র প্রসাদ যাচ্ছেন শুনে অসন্তুষ্ট হন নেহরু। নেহরুর যুক্তি ছিল, রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজেন্দ্র প্রসাদ শুধুমাত্র হিন্দুদের নন, সমস্ত ভারতীয়দের প্রতিনিধি। তাই রাজেন্দ্রপ্রসাদের মন্দির উদ্বোধনে যাওয়া, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার কথা জানতে পেরে অবাক হয়েছিলেন।
নেহরুর ভারত ভাবনাকে বুঝতে হলে, বিশ্বমঞ্চে ভারতকে তুলে ধরার তাঁর ভাবনাকে বুঝতে হবে। ইদানীং কালে মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের একটি বড় অংশের মধ্যে নেহরুকে নিয়ে বৈরিভাব তৈরি হয়েছে। তাই নেহরুর ভারত-ভাবনাকে বোঝা এবং তার মূল্যায়ন কার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ ইদানীং মধ্যবিত্তদের মধ্যে হিন্দু অধিকার জাহিরের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। তাই প্রায়শই বলা হয় যে, নেহরুর আমলের ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল। এমনকি এমন কল্পকথাও রয়েছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের আসন পাওয়া নাকি পাকা হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু চিনকে সেই আসন ছেড়ে দেন নেহরু। তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর পরিবর্তে বিনা প্ররোচনায় ১৯৬২ সালে ভারতকে আক্রমণ করে চিন। রাষ্ট্রপুঞ্জের আসন ছেড়ে নেহরু ‘মুর্খামি’র পরিচয় দেন এবং তার পরের ঘটনাবলীই তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় বলেও দাবি করেন কেউ কেউ। কিন্তু আসল কথা হল, ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী গান্ধী খুন হওয়ার পর আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন নেহরুই। আজও কেউ নেহরুর উচ্চতায় পৌঁছতে পারেননি। সাধারণ ভারতবাসীর জীবনে নেহরুর যা প্রভাব ছিল, আজও কেউ তার ধারেকাছে আসতে পারেননি। শুধুমাত্র পশ্চিমি আদব-কায়দা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, বিদ্বান এবং ভদ্রলোক সুলভ আচরণের জন্য তা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক মহলে নিজের দর বাড়াতেই নেহরু খ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন বলে দাবি করেন নিন্দুকেরা। আসল কথা হল, ঐক্য় এবং উদারতার নীতিই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন থেকে পল ও এসি রোবসন হোন বা ল্যাংস্টন হিউজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে পোক্ত করে তোলে। জীবিতকালে একাধিক বার নেহরুর প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলাকেও।
নেহরুর শাসনকালের কথা উঠলেই, সই সময় বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের স্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। কিন্তু আজকের দিনে ‘গ্লোবাল সাউথ’ বলে যে ধারণা রয়েছে, তাতে ঔপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে অন্য দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংহতি এবং যোগসূত্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই ধারণাটি আদতে নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। ঔপনিবেশিক এবং অশ্বেতাঙ্গ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগসাধনের পক্ষে ছিলেন নেহরু, যাতে পশ্চিমের শক্তিধর রাষ্ট্র এই দেশগুলিকে পদদলিত করতে না পারে। ১৯৫৫ সালে আয়োজিত বানদুং কনফারেন্স অফ এশিয়ান অ্যান্ড আফ্রিকান কান্ট্রিজ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নেহরুর। সেখানে তিনিই ছিলেন আন্তর্জাতিক মহলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ। নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসূত অসহযোগ নীতি সেখানে মাইলফলক হয়ে ওঠে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় না আমেরিকা, না সোভিয়েত ইউনিয়ন (অধুনা রাশিয়া) কারও সঙ্গে মিত্রতায় যাননি নেহরু। স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতকে এমন একটি দেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন নেহরু। যদিও পরিস্থিতি ভূ-রাজনৈতিক জটিলতার কারণে, বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রায়শই রাশিয়ার পক্ষ নিতে হয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। তবে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অনুপ্রেরণাতেই নেহরু আন্তর্জাতিক রাজননীতিতে তৃতীয় বিকল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ভয়াবহ ইতিহাস, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকলে, তার বাস্তবায়ন অসম্ভব ছিল না। আবার গান্ধীর একনমিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন বলেই, রাজনীতির জগতের বাসিন্দা হয়েও কখনও নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিতে পারেননি।